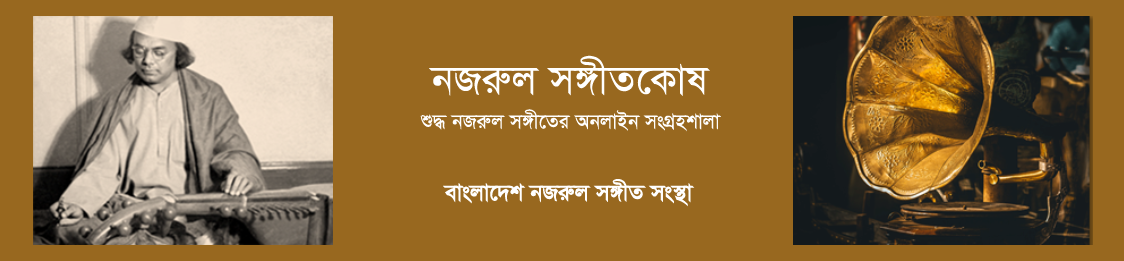আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিনামে লুচি (amar horiname ruchi karon poriname luchi)
তাল: ফেরতা (দাদরা-কাহারবা)
আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিনামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।
আমি মালপোর লোভে এ কল্প-লোকে তল্পি বাঁধিয়া এসেছি মন॥
‘রাধাবল্লভি’-লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
আসি রস-গোল্লার তরে রাস-মোচ্ছবে!
আমার গোল্লায় গেছে মন দাদা গো রস-গোল্লায় গেছে মন!
ও তো রসগোল্লা কভু নয়
যেন ন্যাড়া-মাথা বাবাজি থালাতে হয়েন উদয়!
(আর) গজা দেখে প্রেম যে গজায় হৃদিতলে রে,
পানতোয়া দেখে প্রাণ নাচে হরি বলে রে!
ঐ গোলগাল মোয়া এই মায়াময় সংসার দেয় গো ভুলিয়ে,
আর ক্ষীরের খোয়াতে খোয়াইতে কুল মন ওঠে চুলবুলিয়ে!
(আমার) মন বলে হরি হরি হাত বলে হরো হে
যত অরসিকে তেড়ে আসে বলে ব্যাটায় ধরো হে!
আর এই সংসারে রসিক শুধু রাঁধুনী ও ময়রাই–
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!
যারা ময়দা পেয়ে মালপো ঢালে
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!
আমি চিনি মেখে গায়ে যোগী হব দাদা যাব ময়রার দেশে
আর রসকরার কড়াই-এ ডুবিয়া মরিব গলে সন্দেশ ঠেসে।
ভোজন-ভজহরির শোনো এই তথ্য গো-ময় সংসারে ভোজনই সত্য॥
- ভাবসন্ধান: এই গানে কপট বৈষ্ণব ধর্মাচারীর অভিব্যক্তি রঙ্গ-ব্যঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। লোক দেখানো রাধকৃষ্ণের ভক্তির আড়ালে ভক্তের পার্থিব লোভ লালসার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে এই গানে। এই গানে কবি ব্যঙ্গার্থে শব্দলীলায় তৈরি করেছেন ছোটো ছোটো রূপকল্প। শব্দের ধ্বনিগত এবং অর্থগত রূপ নিয়ে অবলীলায় লীলা করেছেন। এই গানে মূল তথ্য- জগতের সব কিছুই অসার, অলীক। একমাত্র সার ও সত্য হলো ভোজন।
এই গানের ভক্তের ভজনের লক্ষ্য ধর্মীয় মোক্ষলাভ নয়, ভোজনই তার মোক্ষ। তার কাছে হরিনাম রুচির চেয়ে, নামকীর্তন শেষে পাওয়া পেট-পূজার উপকরণ লুচি মহার্ঘ্য। ভক্ত দেবমন্দিরে মালপোর লোভে তল্পি বেঁধে চলমান কল্পলোকে এসেছে। ভক্ত রাধার বল্লভ অর্থে কৃষ্ণকে পূজা করতে এসেছে রাধাবল্লভী নামক খাবারের লোভ। তার রসগোল্লার মোহে গোল্লায় গেছে মন, তাই সে রাধাকৃষ্ণের রাসোৎসবে আসে রসগোল্লার লোভে। তার কাছে মনে হয়, গোল্লা ন্যাড়া-মাথা বাবাজি (চৈতন্যদেবের টাক মাথার তুল্য ) হয়ে যেন থালাতে হাজির হয়।
ভোগের গজা দেখে ভক্তের মনে জাগে গজাপ্রীতি আর পানতোয়া দেখে তার প্রাণ নেচে ওঠে
হরি নামকীর্তনের উল্লাস। মোয়ার গোলগাল অবয়ব দেখে সে ভুলে যায় সংসার মায়া, আর ক্ষীরের খৈ তার কুল-ঐতিহ্য ভুলিতে আকুলিবিকুলি করে ওঠে তার মন।
তাই তার মন হরি বললেও, তার হাত তাকে খাদ্য হরণে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু অরসিক জনে তা বুঝতে চায় না। তাই চোর চোর বলে তার দিকে তেড়ে আসে। ভক্তের কাছে মনে হয়, এই জগৎসংসারে একমাত্র রসিক-জন হলো রাধুনী আর মিষ্টি তৈরির কারিগররা। এরা দুজনই কৃষ্ণের নৈবেদ্য তৈরি জন্য এসেছে। এরা দুই ভাই মিলে ময়দা দিয়ে মালপো বানায়। ভক্তি মিষ্টির আশায়- নিজেই গায়ে চিনি মেখে ময়রার কাছে যোগীর বেশে যেতে চায়। কারণ সেখানে সে রসের কড়াইতে ডুবে মরতে চায় গলায় সন্দেশ পুরে।
ভক্তি ভনিতায় নিজেকে ভোজনের ভজহরি আখ্যায়িত করেছে। তার মতে- সংসার গরুর মতো নির্বোধ ও অসত্য। সেখানে এখানে একমাত্র সত্য হলো ভোজন।
- রচনাকাল ও স্থান: গানটির রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় (জুলাই ১৯৩২) মাসে প্রকাশিত ' সুর-সাকী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় নজরুলের বয়স ছিল ৩৩ বৎসর ১ মাস।
- গ্রন্থ:
- সুর-সাকী
- প্রথম সংস্করণ [আষাঢ় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। জুলাই ১৯৩২)]
- নজরুল রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। [জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মে ২০১১। সুর-সাকী। ৯৭ সংখ্যক গান। কীর্তন। পৃষ্ঠা ২৮৫-২৮৬]
- নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ,[নজরুল ইনস্টিটিউট, মাঘ ১৪১৮। ফেব্রুয়ারি ২০১২। সংখ্যা ২৩৫৫। তাল: ফেরতা (দাদরা-কাহারবা)। পৃষ্ঠা: ৭১৬]
- সুর-সাকী
- রেকর্ড: টুইন [নভেম্বর ১৯৩২ (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)। এফটি ২২৯০। শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[শ্রবণ নমুনা]
- পর্যায়:
- বিষয়াঙ্গ: ধর্মসঙ্গীত। বৈষ্ণব-সঙ্গীত। রঙ্গব্যঙ্গ