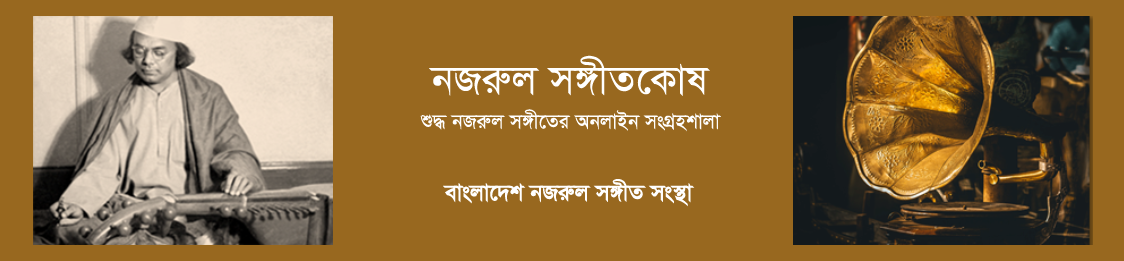আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি। (amare chokh esharay dak dile hay ke go dorodi)
আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি।
খুলে দাও রং মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি॥
গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েলা ননদী॥
পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥
তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি॥
পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুঁহু হায় চাই বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি॥
ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর কবি
ঊষসীর শিশ্-মহলে আস্তে যদি চাস্ নিরবধি॥
- ভাবসন্ধান: সুফিবাদী দর্শনে রচিত এই গানে ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে প্রকতির অপার সৌন্দর্যদর্শনের সৌভাগ্যে। বিশ্বসংসারের অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে কবি অপাঙ্ক্তেয় ছিলেন। পরমসৌন্দর্যেধারী কবিকে করুণা করে, চোখের ঈঙ্গিতে সে সৌন্দর্য দর্শনের জন্য ডাক দিয়েছেন, কিন্তু উপভোগের উপযোগী দর্শনের চোখ খুলে দেন নি। তাই কবি সে অজানা রহস্যময় আহবানকারীর কাছে সকাতর অনুযোগে বলছেন- রঙ-মহলায় ডাকলেই যদি, তবে তার দ্বার কেন খুলে দিলে না।
কবি মনে করেন এই পরমসৌন্দর্যের অধিকারী পরমসত্তা, চৈতালি হাওয়াকে দিয়ে গোলাপবনে গোপন বারতা পাঠায়, তাই গোলাপ-বন রূপ-সৌগন্ধে বিকশিত হয়। আর তাই দেখে কোকিল ঈর্ষান্বিতা ননদীর মতো কু কু (মন্দ মন্দ) রবে নিন্দা জ্ঞাপন করে। বৈশাখে তাঁরই গোপন বার্তা আনে কপোতীরূপী ঝড়, আর এই ভরষায় কবির কাছে যেন বর্ষায় জলভরা নদী আশ্বাস চায়। তাঁর গোপন অশ্রুই শরতের শিউলি ফুলকে শিশিরে সিক্ত করে। তিনি প্রকৃতির ঘুম ভাঙানিয়া দ্বার রুদ্ধ করে হেমন্তের শীতল পরশ বুলিয়ে দেন। তাঁরই ইশারায় পৌষের শস্যহীন মাঠে, নির্জন পথের পানে চেয়ে কবির মতই কোনো এক বিরহণীর বিষাদে কাতর হয়, উভয়ের কামনার ভিতরে সাগরতুল্য কান্না উথলিত হয়।
এতসব রূপবৈচিত্র্যের লীলায় কবি যেন বিভ্রান্ত। গানের শেষ পঙ্ক্তিতে সৌন্দর্যপিপাসু ভ্রমর কবি স্বগোক্তিতে নিজেকেই শোনান- যদি এই ভোরের সুরভিত সৌন্দর্যের খাসমহলে সর্বদা তিনি আসতেই চান, তাহলেই রূপবৈচিত্র্যের আনন্দ-বেদনার লীলার কথা না ভেবেই আসতে হবে। শেষ পঙক্তিতে কবি যেন নিজেকেই রঙমহলের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য নিজেকেই তাড়িত করেন। রহস্যময় সৌন্দর্যসত্তা কেন- রঙমহলের দ্বারা তাঁর সামনে অবারিত করেন না, তারও মীমাংশা ঘটে গানের শেষে।
এই গানের 'ভ্রমর কবি' ভণিতার সূচনা হয়েছিল- কবির ১১-১৩ বৎসর বয়সের ভিতর রচিত লেটো গানে। গজলাঙ্গের আদলের রচিত এই গানের কবি হয়ে উঠছেন 'ভ্রমর কবি' ভণিতায়।
- রচনাকাল ও স্থান: গানটির রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। উল্লেখ্য, কল্লোল পত্রিকার 'চৈত্র ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ' সংখ্যায় (মার্চ, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ) গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ধারণা করা হয়, নজরুল এই গানটি রচনা করেছিলেন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। এই বিচারে ধারণা করা যায়, গানটি রচনার সময় নজরুলের বয়স ছিল ২৭ বৎসর ৮ মাস।
- গ্রন্থ:
- বুলবুল
- প্রথম সংস্করণ [কার্তিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ১৯২৮)। গান ২। জৌনপুরী-আশাবরী─কাহারবা]
- নজরুল-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড [বাংলা একাডেমী, ফাল্গুন ১৪১৩। ফেব্রুয়ারি ২০০৭। বুলবুল। গান ২। জৌনপুরী-আশাবরী─কাহারবা। পৃষ্ঠা: ১৫১-১৫২]
- নজরুল গীতিকা
- প্রথম সংস্করণ [ভাদ্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। গজল। ১১। জৌনপুরী-আশাবরী। পৃষ্ঠা ৬৭]
- নজরুল রচনাবলী, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ। তৃতীয় খণ্ড [বাংলা একাডেমী, ঢাকা ফাল্গুন ১৪১৩/মার্চ ২০০৭।] নজরুল গীতিকা। ৫৬। গজল। জৌনপুরী-আশাবরী। পৃষ্ঠা: ২০৯।
- বুলবুল
- পত্রিকা:
- রেকর্ড: এইচএমভি [সেপ্টেম্বর ১৯২৮ (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৪)। পি ১১৫১৮। শিল্পী: কে. মল্লিক। সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম] [শ্রবণ নমুনা]
- সুরকার: কাজী নজরুল ইসলাম।
- স্বরলিপিকার ও স্বরলিপি: সুধীন দাশ। [নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি, পঞ্চম খণ্ড। কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা] দ্বিতীয় গান। পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩। [নমুনা]
নজরুলের জীবদ্দশায় তাঁর গানের যে সুর-বিকৃতি চলছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট (শুক্রবার, ৭ ভাদ্র ১৩৩৬) নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে তিনি এই বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছলেন। এই চিঠিতে বেতারে প্রচারিত [২৩ আগষ্ট ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ [নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র]
এই পত্রে এই গানটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন-
'...আর একদিন একজন রেডিও স্টার (মহিলা) আমার 'আমারে চোখ ইশারায়' গানটার ন্যাজামুড়ো হাত পা নিয়ে এমন করে তাল গোল পাকিয়ে দিলেন যা দেখে মনে হল বুঝি বা গানটার ওপরে একটা মটোর লরি চলে গেছে। ...'